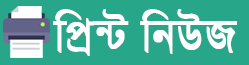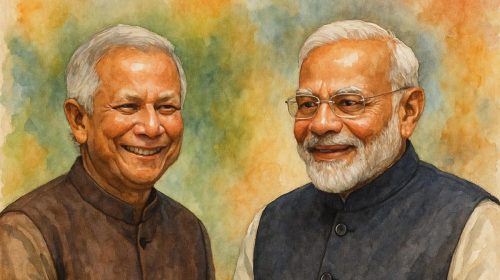ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হয় বাংলাদেশের রাজনীতির জন্মভূমি। এখানকার ক্যাম্পাস থেকেই রাজপথে নেতৃত্ব দিয়েছে বিভিন্ন সময়ের ছাত্র আন্দোলন। মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে ৯০-এর দশকের গণআন্দোলন—সবক্ষেত্রেই ডাকসু নির্বাচন একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখেছে। তাই ডাকসু নির্বাচন সবসময়ই কেবল শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব নয়, বরং দেশের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক দিকনির্দেশনারও প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে।
সাম্প্রতিক ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ভরাডুবি তাই শুধু একটি নির্বাচনী ফল নয়, বরং একটি প্রতীকী সংকেত। ছাত্রদল একসময় ক্যাম্পাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী সংগঠনগুলোর একটি হলেও এখন তারা নানাভাবে হোঁচট খাচ্ছে। এবারের ভরাডুবি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা আলোচনা হচ্ছে। অনেকেই মনে করেন, বহিরাগত চাপ, প্রশাসনের ভূমিকা বা ৫ আগস্টের পর বিএনপির বিতর্কিত অবস্থান এর কারণ হতে পারে। তবে বিশ্লেষক মহলের অভিমত—সবচেয়ে বড় কারণ ছিল ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, নেতৃত্ব সংকট এবং ব্যক্তিস্বার্থের রাজনীতি।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি দেশের ইতিহাসে সবসময় বিশেষ গুরুত্ব বহন করেছে। ডাকসুর ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এখান থেকেই জাতীয় রাজনীতির অনেক নেতার উত্থান ঘটেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান থেকে শুরু করে জিয়াউর রহমান-প্রণব মুখার্জি—সবাই কোনো না কোনোভাবে ছাত্ররাজনীতির মাধ্যমে নেতৃত্বের চর্চা করেছেন।
একসময় ছাত্রদল ছিল ক্যাম্পাসের প্রধান শক্তি। আশির দশক ও নব্বইয়ের দশকে তারা ছাত্র আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৯০ সালের গণআন্দোলনে ছাত্রদলসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা সামরিক শাসন পতনে বড় ভূমিকা রাখে। কিন্তু গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর ছাত্রদলের কার্যক্রম ধীরে ধীরে সীমিত হয়ে আসে।
এখনকার বাস্তবতা হলো—ছাত্রদল প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে। অনেক দিন ধরে তাদের কার্যকর উপস্থিতি দেখা যায়নি ক্যাম্পাসে। কেন্দ্রীয় রাজনীতিতে বিএনপির যে স্থবিরতা, তার প্রতিফলন ছাত্রদলেও স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান।
বিশ্লেষকদের মতে, এবারের ভরাডুবির সবচেয়ে বড় কারণ ছাত্রদলের নেতৃত্ব সংকট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি গণেশ চন্দ্র সাহস নাকি চাননি তাঁর বাইরে কেউ ভিপি বা জিএস পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক। নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হলে তাঁর প্রভাব কমে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই তিনি নাকি দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন।
এই কারণে শুরু থেকেই ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল অংশ নেবে কি না, তা অনিশ্চিত ছিল। যখন প্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠনগুলো ক্যাম্পাসে পোস্টার টানছে, শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ করছে, তখনো ছাত্রদল প্যানেল ঘোষণাই করতে পারেনি। অবশেষে ভোটের মাত্র ২০ দিন আগে প্যানেল ঘোষণা করে। ততদিনে তাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ে।
প্রার্থীরা কারা হবেন, সেটি নিয়েও ভেতরে ভেতরে দোটানা ছিল। অনেকে মনে করেছিলেন, যদি যোগ্য ও জনপ্রিয় মুখকে প্রার্থী করা হতো, তাহলে ফল ভিন্ন হতে পারত। কিন্তু সেখানে দলের ভেতরকার দ্বিধা ও ব্যক্তিস্বার্থই বড় হয়ে ওঠে।
ডাকসু নির্বাচনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে হলে আগে থেকেই প্রস্তুতি, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জনের কৌশল থাকা জরুরি। ছাত্রদলের সেই প্রস্তুতি ছিল না বললেই চলে।
প্রচার-প্রচারণার সীমাবদ্ধতা: তাদের প্রচারণায় তেমন কোনো নতুনত্ব ছিল না। পোস্টার, লিফলেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও খুব কম সক্রিয়তা দেখা গেছে।
ইশতেহারের দুর্বলতা: যে বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—হোস্টেল সংকট, পরিবহন ব্যবস্থা, লাইব্রেরি উন্নয়ন, নিরাপত্তা—এসব ইস্যুতে তারা স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে।
কৌশলগত ব্যর্থতা: অন্য সংগঠনগুলো যখন শিক্ষার্থীদের কাছে বারবার পৌঁছে গেছে, ছাত্রদলের প্রার্থীরা তখনও নিজেদের মধ্যে ব্যস্ত ছিল।
ফলে তাদের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ তৈরি হয়নি।
একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য—জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে ছাত্রশিবির যেভাবে তাদের দুই নেতা আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদকে সামনে এনেছে, সেভাবে ছাত্রদল কাউকে তুলতে পারেনি। ক্যাম্পাসে দৃশ্যমান নেতৃত্ব গড়ে তুলতে ব্যর্থ হওয়ায় ভোটাররা তাদেরকে গুরুত্ব দেয়নি।
এটি প্রমাণ করে, রাজনীতিতে শুধু অতীতের ঐতিহ্য দিয়ে চলা যায় না; বর্তমান প্রজন্মকে আকৃষ্ট করতে হলে দৃশ্যমান কার্যক্রম ও নেতৃত্বের প্রয়োজন।
ছাত্রদলের ভেতরে বহুদিন ধরেই গ্রুপিং চলছে। একাধিক উপগোষ্ঠী নিজেদের মতো করে সংগঠন চালাচ্ছে। এতে ঐক্যহীনতা প্রকট হয়ে ওঠে। নির্বাচনী সময়েও এর প্রভাব পড়েছে।
একেকজন প্রার্থী একেক ধরণের প্রচারণা চালিয়েছে।
কেন্দ্রীয় দিকনির্দেশনার অভাব ছিল।
কর্মী-সমর্থকরা বিভ্রান্ত হয়েছে, কাকে অনুসরণ করবে বুঝতে পারেনি।
এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই মূলত প্যানেলকে দুর্বল করে দিয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে কথা বললে হতাশার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাদের বক্তব্যগুলোতে কিছু মিল পাওয়া যায়—
“তাদের কোনো পরিকল্পনা নেই। শুধু অতীতের স্লোগান শুনিয়েছেন।”
“আমরা ভেবেছিলাম অন্তত একাডেমিক সমস্যা নিয়ে কিছু বলবেন, কিন্তু সেটা হয়নি।”
“৫ আগস্ট-পরবর্তী সময়ে অন্যান্য সংগঠন যে কর্মসূচি নিয়েছে, ছাত্রদল তার অর্ধেকও করতে পারেনি।”
এ থেকেই বোঝা যায়, শিক্ষার্থীরা ছাত্রদলের উপর আস্থা রাখতে পারছে না।
নির্বাচনের পর অনেক সংগঠন বহিরাগত কারণ খোঁজে। প্রশাসনের পক্ষপাতিত্ব, প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রভাব ইত্যাদি যুক্তি তুলে ধরে। ছাত্রদলও হয়তো তাই করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো—তাদের ভরাডুবির প্রধান কারণ নিজেরাই।
যদি নেতৃত্ব সংকীর্ণ মানসিকতার কারণে নতুন কাউকে জায়গা না দেয়, যদি প্রস্তুতির অভাব থাকে, যদি শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জনের মতো কার্যক্রম না থাকে—তাহলে জয় আসবেই না।
ছাত্রদলের এই ব্যর্থতা কেবল একটি সংগঠনের সমস্যা নয়। জাতীয় রাজনীতিতেও এর প্রভাব পড়বে। কারণ ডাকসু থেকে যে নেতৃত্ব তৈরি হয়, সেটাই ভবিষ্যতের জাতীয় নেতৃত্ব। যদি ছাত্রদল এখানেও ব্যর্থ হয়, তবে বিএনপির জন্যও ভবিষ্যতে বড় সংকট তৈরি হবে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন—
“ছাত্রদল যদি নিজেদের ভেতরে সংস্কার না আনে, তবে তারা ক্রমেই প্রান্তিক হয়ে যাবে। বিএনপির কেন্দ্রীয় রাজনীতির জন্য এটি ভয়াবহ সংকেত।”
এখন ছাত্রদলের সামনে দুটি পথ—
আত্মসমালোচনা করে নিজেদের দুর্বলতা চিহ্নিত করা।
অন্যদের ওপর দায় চাপিয়ে আগের মতো চলতে থাকা।
প্রথম পথটি গ্রহণ করলে হয়তো তারা ধীরে ধীরে আস্থা ফিরে পাবে। কিন্তু দ্বিতীয় পথ বেছে নিলে তাদের ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হবে।
ছাত্রদল যদি টিকে থাকতে চায়, তাহলে কয়েকটি বিষয় জরুরি—
গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ফিরিয়ে আনা – নেতৃত্ব নির্বাচনে স্বচ্ছতা আনতে হবে।
যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন – যারা ক্যাম্পাসে সক্রিয় ও জনপ্রিয়, তাদের প্রার্থী করতে হবে।
ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি – শিক্ষার্থীদের বাস্তব সমস্যার সমাধানকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
সংগঠনগত ঐক্য – অভ্যন্তরীণ বিভক্তি দূর করতে হবে।
দীর্ঘমেয়াদী কৌশল – নির্বাচনের আগে নয়, সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীদের পাশে থাকতে হবে।
নতুন প্রজন্মকে আকৃষ্ট করা – সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ও শিক্ষাবান্ধব কর্মসূচি নিয়ে এগোতে হবে।
ডাকসু নির্বাচন শুধু ভোট নয়; এটি দেশের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনের ক্ষেত্র। ছাত্রদলের এবারের ভরাডুবি তাই কেবল একটি পরাজয় নয়, বরং একটি সতর্কবার্তা।
অতএব, ডাকসু নির্বাচনে ছাত্রদলের ভরাডুবির দায় বহিরাগত নয়, বরং নিজেদের কাঁধেই। এখন প্রশ্ন হলো—তারা কি আত্মসমালোচনা করে নতুন পথ খুঁজবে, নাকি আগের মতো দায় চাপিয়ে আরও পিছিয়ে যাবে?